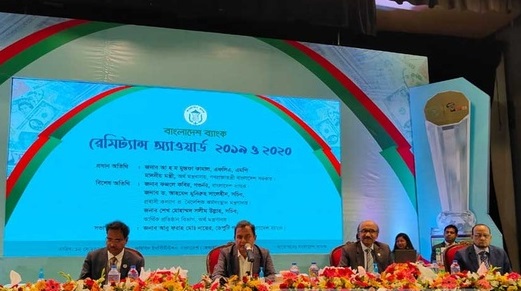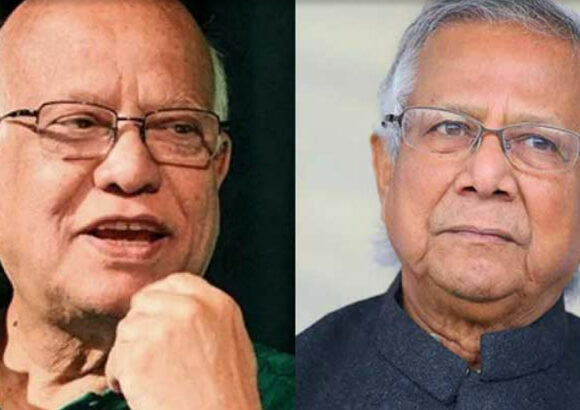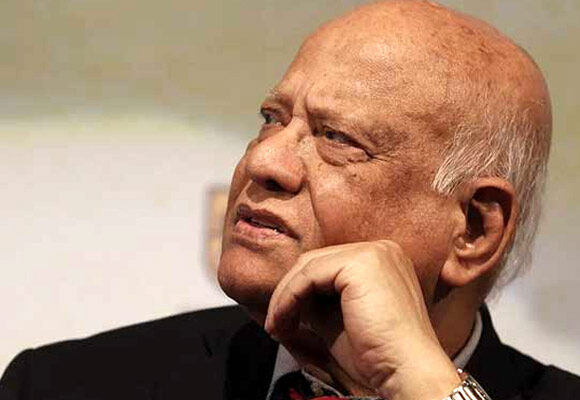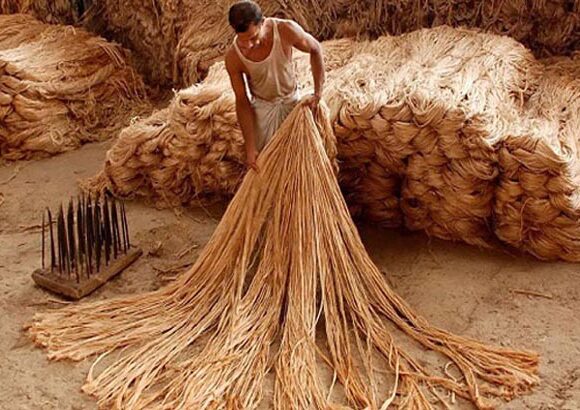দেশ থেকে যে অর্থ পাচার হয়েছে, তা ফিরে আসবে বলে বলে আশায় আছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।
তবে কী পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে, তার কোনো হিসাব তার কাছে নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।
দেশ থেকে অর্থ পাচার বরাবরই্ আলোচনার বিষয় হয়ে থাকছে। হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে বিরোধী রাজনীতিকরা বলে আসছেন।
গত বছর ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালেই বাংলাদেশ থেকে ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়।
বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় সোয়া ৪ লাখ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ।
বৃহস্পতিবার প্রবাসীদের সম্মাননা দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯-২০ প্রদান অনুষ্ঠানে অর্থ পাচারের প্রসঙ্গটি আসে।
ব্যবসায়ী ক্যাটেগরিতে সম্মাননা পাওয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবাসী ওমর ফারুক অনুষ্ঠানে বলেন, “বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার যাচ্ছে, বিনিয়োগ হচ্ছে। এসব অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।”
তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী বলেন, “আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই অর্থ নিয়ে চলে যাওয়ার। আমরাও শুনছি। পৃথিবীর কয়েকটি দেশ আছে যারা অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেয়, সংযুক্ত আরব আমিরাতও সেরকম। সেখানে শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্যান্য দেশ থেকেই অর্থ যায়।
“আমরা এগুলো শুনি। কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই আমাদের কাছে। ফরমাল চ্যানেলের বাইরে (ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে) অর্থ লেনদেন কোনো এক সময়ে প্রশ্ন তৈরি করবে। তবে আমরা একটা আশা নিয়ে আছি। সেটা বড় আশা। টাকা যেগুলো যাচ্ছে ..তা আবার ফিরে আসবে। আমরা এমনভাবে সুবিধা দেব, সবাই ফিরে আসবে বাংলাদেশে।”
প্রবাসীরা প্রস্তাব করেন, ওয়েজ আর্নার বন্ড কেনার সীমা তুলে দিয়ে এর অর্থ বিনিয়োগ শেষে ফেরত নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার। বর্তমানে একেজন প্রবাসী সর্বোচ্চ এক কোটি টাকার ওয়েজ আর্নার বন্ড কিনতে পারেন।
এক্ষেত্রে আশ্বাস দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, “আমরা ধীরে ধীরে ডলার হিসাব ওপেন করছি। ওয়েজ আর্নার বন্ডের অর্থ ফেরত নিয়ে যাওয়া আর সীমা তুলে নেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করব।”
প্রবাসীদের রেমিটেন্স ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, “ব্যাংকের বাইরে পাঠানো রেমিটেন্স কিন্তু নিরাপদ নয়। রেমিটেন্স পেতে আমরা সবকিছু করব। এখন আমাদের রেমিটেন্স বড় প্রয়োজন।”
মূল্যস্ফীতি ও সরকারের ঋণ নিয়ে মুস্তফা কামাল বলেন, “মূল্যস্ফীতি আন্তর্জাতিকভাবে হচ্ছে। সারা বিশ্বে একই অবস্থা। কিন্তু আমরা সফল হব। বর্তমানে ঋণ-জিডিপির অনুপাত ৩৪ শতাংশ। সবই সহজ শর্তের ঋণ। আমাদের কোনো হার্ড ঋণ নেই। তাই সমস্যা হবে না।”
কোভিড মহামারীতে ২০১৯ সালে রেমিটেন্স পাঠানো প্রবাসীদের সম্মাননা দিতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক। এবার ২০১৯ ও ২০২০ সালের জন্য পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী ক্যাটেগরিতে ৫৩ জন ও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এক্সচেঞ্জ হাউস এবং ব্যাংক মিলিয়ে ৬৭টি পুরস্কার দেওয়া হয়।
প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোয় উৎসাহ দিতে ২০১৪ সাল থেকে রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৯৯ জনকে সম্মাননা দেওয়া হয়।
ঢাকার ফার্মগেইট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনের এই অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ছিলেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির।
গভর্নরও প্রবাসীদের রেমিটেন্স ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানোর আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, “প্রবাসীদের জন্য ডলার ইনভেস্টমেন্ট ও প্রিমিয়ার ডলার বন্ড রয়েছে বিনিয়োগ করার। সেখানে বিনিয়োগ করতে পারেন। যা দেশীয় ব্যাংকের সুদহারের চেয়ে বেশি।”
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, “রেমিটেন্স আহরণে অগ্রণী ব্যাংক তৃতীয় অবস্থানে। এক সময়ে দ্বিতীয় ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার কারণে রেমিটেন্স আনতে পারছি না।
“প্রতিযোগিতার বাজারে সকলের জন্য এক রেট বা আমদানি-রপ্তানি রেটের বাইরেও ডলার আনার সুযোগ দেওয়া উচিৎ।”
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু ফারাহ মো. নাছেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সচিব শেখ মোহম্ম্মদ সলীম উল্লাহও বক্তব্য রাখেন।